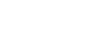ঢাকা: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, দেশের মানুষের জন্য, দেশের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিংয়ের বিখ্যাত “আই হ্যাভ আ ড্রিম“ ভাষণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তারেক রহমান ...
- ‘দ্য লাস্ট লেটার’: ডেনমার্কে বন্ধ হচ্ছে ৪০০ বছরের চিঠি বিলির সংস্কৃতি
- মারা গেছেন বিখ্যাত ফিলিস্তিনি পরিচালক-অভিনেতা মোহাম্মদ বাকরি
- দাদা-দাদির কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করলেন রুমিন ফারহানা
- টাইটেল স্পন্সরহীন বিপিএল
- দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে আমার পরিকল্পনা আছে: তারেক রহমান
- দল চালাতে অপারগ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক, চট্টগ্রামের দায়িত্ব নিল বিসিবি
- বড়দিনের শুভেচ্ছায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের গালাগাল করলেন ট্রাম্প
- এনসিপির জোটে ফাটল
- প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বকশ চৌধুরীর পদত্যাগ
- হাদি হত্যাকাণ্ড: খুনিকে পালানোর ব্যবস্থা করেন যুবলীগের তাইজুল
সব খবর >>
মতামত
সাক্ষাৎকার
সারাবাংলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: দাদা-দাদির কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ-বিজয়নগর একাংশ) আসনে নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেছেন দলীয় মনোনয়নবঞ্চিত হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহসম্পাদক রুমিন ফারহানা।বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজয়নগর উপজেলার বুধন্তি ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামে দাদা-দাদির কবর ...বিস্তারিত
বিনোদন

স্বনামধন্য ফিলিস্তিনি অভিনেতা ও পরিচালক মোহাম্মদ বাকরি (৭২) গত বুধবার মারা গেছেন। তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। বৃহস্পতিবার তার পরিবারের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন।গতকালই ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে নিজ জন্মস্থান আল-বাই'নেহ শহরে সমাধিস্থ হন ...বিস্তারিত
লাইফস্টাইল

দেশে গত সাড়ে ৩১ ঘণ্টায় চারবার ভূমিকম্প হয়েছে। এর মধ্যে আজ শনিবার সকালে একবার ও সন্ধ্যায় পরপর দুবার ভূকম্পন অনুভূত হয়। এর আগে গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাজধানীসহ আশপাশের এলাকা।শুক্রবারের ...বিস্তারিত
শিল্প-সাহিত্য
 ‘যারা কম বোঝে, তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী’
‘যারা কম বোঝে, তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী’নন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন বহুমাত্রিক শিল্পস্রষ্টা। গল্প বলার ভাষা আর ভঙ্গিকে আরও সহজ, আরও জীবন্ত করেছেন তিনি। তাঁর লেখায় সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না, স্বপ্ন-বাস্তবতা আর জীবনের টানাপোড়েন এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে ...বিস্তারিত
স্পটলাইট
পানি চাই-পানি। পানির অপর নাম জীবন। তাই ‘তরল সোনা’ বলে খ্যাতি আছে যে তেলের তার বিনিময়ে ...
আর্কাইভ সংবাদ